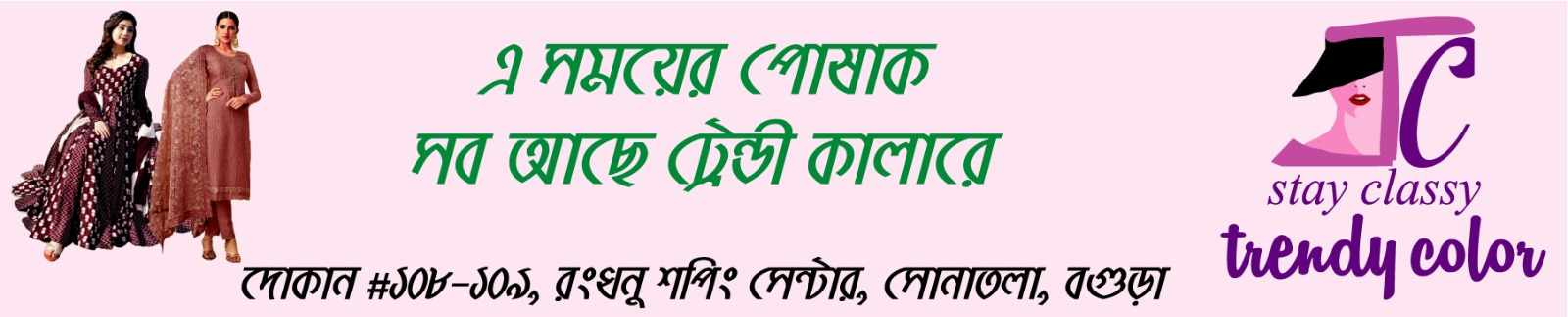‘ওকে হোটেল’ ঢাকার প্রথম হোটেল ও রেস্তোরাঁ। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ ও বিদেশি পর্যটকেরা বাণিজ্যিক বা প্রশাসনিক কাজে ঢাকায় এলে সরকারি বাংলো বা অতিথিশালায় থাকতেন। ঢাকায় কোনো হোটেল ছিল না। ঢাকার জনসন রোডে বর্তমান আজাদ সিনেমার পাশে ওকে হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের আবির্ভাব ঘটে। বিদেশি অতিথি ও পর্যটকদের আবাসস্থল হিসেবে ওকে হোটেলের নাম ছিল।
অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হোটেলটি যাত্রা শুরু করে। আবার অনেকের অভিমত, হোটেলটি ত্রিশের দশকের মাঝামাঝিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মালিক ছিলেন একজন স্কটিশ, তিনি কলকাতা থেকে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন।
ডলি জোন্সকে আজিম বখশ আন্টি বলে ডাকতেন। ডলির বাবার নাম ছিল রবার্ট জোন্স, আজিম হলেন মওলা বখশ সরদারের বড় ছেলে। রবার্ট ও মওলা বখশের সম্পর্ক ছিল গভীর। দেশভাগের কিছু আগে বা পরপর রবার্ট ডলিকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। ভাগ্যের উন্নয়নই ছিল উদ্দেশ্য। জজকোর্টের উল্টো দিকে আজাদ সিনেমা হলের পাশে একটি দ্বিতল ভবন তারা লিজ বা ভাড়া নেন। এখানে আগে থেকেই একটি রেস্টুরেন্ট কাম হোটেল ছিল। নাম ছিল ‘ওকে’। এবং ঢাকা গবেষকদের প্রায় সবাই একমত, ওকে ঢাকার প্রথম ইউরোপিয়ান ধারার রেস্তোরাঁ।
সাদ উর রহমান তার ‘ঢাকাই খাবার ও খাদ্যসংস্কৃতি’ গ্রন্থে এ নিয়ে লিখেছেন, ওকে হোটেল ঢাকার প্রথম হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ ও বিদেশি পর্যটকেরা বাণিজ্যিক বা প্রশাসনিক কাজে ঢাকায় এলে সরকারি বাংলো বা অতিথিশালায় থাকতেন। ঢাকায় কোনো হোটেল ছিল না। ঢাকার জনসন রোডে বর্তমান আজাদ সিনেমার পাশে ওকে হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের আবির্ভাব ঘটে। বিদেশি অতিথি ও পর্যটকদের আবাসস্থল হিসেবে ওকে হোটেলের নাম ছিল।
যদিও অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হোটেলটি যাত্রা শুরু করে, কিন্তু এ নিয়ে সাদ দ্বিধাগ্রস্ত। তার অভিমত, হোটেলটি ত্রিশের দশকের মাঝামাঝিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মালিক ছিলেন একজন স্কটিশ, তিনি কলকাতা থেকে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঢাকায় ইউরোপীয়দের উপযোগী কোনো হোটেল ও রেস্টুরেন্ট নেই। অথচ ঢাকা তখন আগের তুলনায় অনেক জমজমাট। প্রতিদিনই সদরঘাটে বজরা ভিড়ছে, প্যাডেল স্টিমার থেকে হ্যাট ও কোট-টাই পরা সিভিলিয়ানরা নামছে। ভিক্টোরিয়া পার্ক বা বাহাদুর শাহ পার্ক ঘিরে বেশ কিছু ব্রিটিশ বসতি, ঢাকা ব্যাংক, জজকোর্ট—সব মিলিয়ে জনসন রোর্ড হার্ট অব দ্য সিটি। জজকোর্টের ঠিক উল্টো দিকে স্কটিশ ভদ্রলোক হোটেলের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করলেন। নাম দিলেন ওকে। পুরোপুরি ব্রিটিশ স্টাইলের হোটেল। ব্রেড, ওমলেট, বাটার, কাঁটা চামচ, প্যাটিস, হ্যাম, চিকেন ফ্রাই, রোল, চপ নিয়ে সেজে উঠল ওকে। জাহাজে করে কলকাতা থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে ওকে হোটেলের চালান আসত। হোটেলে কোনো স্থানীয়ের প্রবেশাধিকার ছিল না। একটি বারও ছিল, যেখানে হার্ড ড্রিংকস পরিবেশন করা হতো। যেহেতু সব ইউরোপীয়ের ডাকবাংলোয় স্থান সংকুলান হতো না, তাই ওকে হোটেল পরিচিতি লাভ করেছিল। পানীয় পানের ব্যবস্থা ছিল বিশেষ আকর্ষণ। রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্টে ভিড় জমে যেত। অনেকে ঘোড়ার গাড়ি বা মোটরকার থামিয়ে নাশতা সেরে তারপর কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন। স্থানীয়রা ভেতরে বসতে না পারলেও গরম গরম পাউরুটি ও মাখন পার্সেল নিতে পারত। মাখনের চাকার গায়ে ‘দেখিয়া ক্রয় করুন’ গোছের সিল মারা থাকত। দ্বিতল ভবনের ওপর তলায় থাকার ঘর আর নিচে ছিল রেস্তোরাঁ। ঢাকাবাসীর দেখার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল ওকে। এখানে কেরোসিনের ফ্রিজ ছিল, বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরত, বাতি জ্বলত। তারপর যুদ্ধ বাধল, এল দেশভাগ। স্কটিশ ভদ্রলোক ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন।
রবার্ট ও তার মেয়ে ডলি এলেন ঢাকায়। অ্যাংলো পরিবারটির আসল ঠিকানা মেঘালয়ের শিলং। তারাও এসেছিলেন ভাগ্য যাচাই করতে। ওকে হোটেলটিকে তারা নিজেদের মতো সাজিয়ে নিলেন। নতুন নাম দিলেন মাইরেন্ডার। দেশভাগের পরের ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী। মারোয়াড়ি, পাঠান, কাবুলি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, ইস্পাহানি তথা অনেক নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন পেশা, নতুন সব ব্যবসা। প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী বলে ঢাকার প্রশাসনিক গুরুত্বও বেড়ে গেছে। তাই সিভিল সার্ভিসের কর্তাব্যক্তিও অনেক। রবার্টরা অবশ্য সবার জন্য মাইরেন্ডারকে উন্মুক্ত করলেন না। তবে স্থানীয় অভিজাতরা ঠিকই সমাদর পেল। বার বহাল রইল আগের মতোই। কাটলেট, ক্র্যাম্প চপ, রোলও তৈরি হতে লাগল। দুপুরে একরকম হলুদ স্যুপ পাওয়া যেতে লাগল, যাকে ‘মুন্নি কি তান্নি’ নামে ডাকা হতো। এর লোভেও অনেকে ভিড় করত। ডলির আকর্ষণেও আসতেন কেউ কেউ। ১৯৭১ সালের ১৫ জানুয়ারি সংখ্যায় দৈনিক পাকিস্তানে লেখা হচ্ছে, এর (মাইরেন্ডার) প্রধান আকর্ষণ ছিল এর মালিক রবার্ট জোন্সের ষোড়শী মেয়ে ডলি জোন্স।
রবার্ট মারা যাওয়ার পর ডলি হোটেলের দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নেন। তিনি খাবার পরিবেশন, তত্ত্বাবধান, অর্থ ব্যবস্থাপনাসহ সব কাজেই নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মাইরেন্ডার ঢাকাবাসীর মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। জনাব সাদ জানালেন, এটি ছিল অভিজাত, কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁ। বেয়ারারা মাথায় পাগড়ি, গায়ে আচকান পরিধান করত। গেস্ট এলে সঙ্গে সঙ্গে সালাম ঠুকত। চেয়ার এগিয়ে পিছিয়ে দিয়ে বসতে সাহায্য করত। মেনু কার্ড ছিল। একটি ইংলিশ রেস্টুরেন্ট যেমন হয়, ওকে তথা মাইরেন্ডার তেমনই ছিল।
ডলির বাবাকে আজিম বখশ (৮০) দেখেননি। কিন্তু ডলির সঙ্গে তার বহুবার দেখা হয়েছে। আজিম যখন এসএসসি পরীক্ষায় বসতে যাবেন, তখন ডলি একটি ফাউন্টেন পেন উপহার দিয়েছিলেন। আজিমের বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। সে বিয়েতে সরদারবাড়ির খোলা আঙিনায় কয়েক শ লোকের জন্য যে টি পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে চায়ের সঙ্গে চপ, বিস্কুট ইত্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছিল ডলির রেস্তোরাঁ মাইরেন্ডার।
ষাটের দশকের শেষ দিকে আজিম বখশ দেখেছেন, মাইরেন্ডারের সদর দরজায় ছিল হাফ সুইং ডোর যেমনটি ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখা যায়। বড় একটা হলঘরের মতো দেখাত রেস্তোরাঁটিকে, কলকাতার কফি হাউজ যেমন। ১০-১২টি টেবিল ছিল, সবগুলো গোলাকার। একেকটি টেবিল ঘিরে ছিল তিন বা চারটি চেয়ার। প্রতিটি টেবিলে টেবিলক্লথ বিছানো থাকত। চা দেওয়া হতো বড় বড় কাপে, ভারী ভারী সিরামিকের থালাবাসন আর বোলে খাবার পরিবেশ করা হতো। ক্যাশ কাউন্টারটি ছিল পেছন দিকে, তারপর ছিল কিচেন। কিচেন শেষ হলে ছিল গাড়ির গ্যারেজ। ডলিদের একটি শ্যাভ্রলে গাড়ি ছিল। গ্যারেজের পরেই ছিল একটি পুকুর।
মাইরেন্ডারের পেস্ট্রিও ছিল উন্নত মানের। তবে ডলিকে একবার তার ভাইয়ের সঙ্গে পিতার উত্তরাধিকার নিয়ে মামলায় জড়াতে হয়েছিল। মওলা বখশ সরদার তখন গৌর মোখতার নামের একজনকে নিযুক্ত করেছিলেন ডলির পক্ষে মামলা তত্ত্বাবধান করার জন্য। আজিম বখশের মনে আছে, সে সময় শেভ্রলে গাড়িটি ভেতরে রেখে গ্যারেজটি সিল করে দেওয়া হয়েছিল। মামলায় অবশ্য ডলিই জিতেছিলেন। সত্তরে যখন বাংলাদেশ স্বাধিকারের দাবিতে উত্তাল, সম্ভবত সে সময় ডলি শিলং ফিরে যান।
তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ডলি আবার ফিরে আসেন জনসন রোডে। কিন্তু আগের মতো ছিল না সবকিছু। ডলিকে আবার টাকা জোগাড়ের জন্য ছুটতে হয়। তখন মওলা বখশ সরদার বেশ কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন। কিছু আসবাবপত্র, থালাবাসন কিনতে হয়েছিল। ভেতরে-বাইরে সংস্কারও করতে হয়েছিল। নতুন দেশে নতুন করে রেস্তোরাঁর নাম রেখেছিলেন আলেকজান্ডার। তিয়াত্তর সালে ডলির বয়স ষাটের আশপাশে। আজিম বখশ বলছিলেন, ‘ভদ্রমহিলা খুব স্টাইলিশ ছিলেন। ফ্রক বা স্কার্ট পরতেন। লম্বা ছিলেন। হিন্দি আর ইংরেজিতে কথা বলতেন। মাঝেমধ্যে ভাঙা বাংলায়। একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যাবতীয় যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল। তিয়াত্তর সালে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি দুটি সুদৃশ্য কাচের গ্লাস এবং একটি ফটো অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন। আলেকজান্ডার অবশ্য মাইরেন্ডারের মতো জনপ্রিয়তা পায়নি। সব আগের মতো ছিলও না। নতুন দেশ, নতুন সবকিছু। আমার যত দূর মনে পড়ে, জলি জোন্স ১৯৭৪ সালেই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান।’
ডলি চলে যাওয়ার পর শাহ কামাল নামে একজন বাঙালি ভদ্রলোক এখানেই একটি হোটেল করেছিলেন। কিন্তু সেটি চলেনি। ভবনটি এখন লইয়ারস চেম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে মাইরেন্ডারের বিশেষ একটি খাবার এখনো ঢাকাবাসীর আদর কাড়ছে, সেটি হলো ক্র্যাম্প চপ। বাংলাবাজারের ক্যাফে কর্নারে খাসির মাংস দিয়ে তৈরি এ সুস্বাদু খাবারটি বিকেলে পাওয়া যায়। মাইরেন্ডারের বাবুর্চি জোসেফ গোমেজ এটি তৈরিতে দক্ষ ছিলেন। মাইরেন্ডার বন্ধ হয়ে গেলে তাকে ক্যাফে কর্নারে নিয়ে আসা হয়। পরে জোসেফের শিষ্য জন গোমেজও ক্র্যাম্প চপ তৈরিতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ক্যাফে কর্নারে যাওয়ার সময় হয় না আজিম বখশের। তবে ক্র্যাম্প চপের ঐতিহ্য ক্যাফে কর্নার ধরে রেখেছে বলে তিনি ভালো বোধ করেন। ডলি আন্টির একটি স্মৃতি এখনো আছে এই শহর ঢাকায়, যা তার কিশোরবেলা আর যুবা বয়সকে ফিরিয়ে আনে।